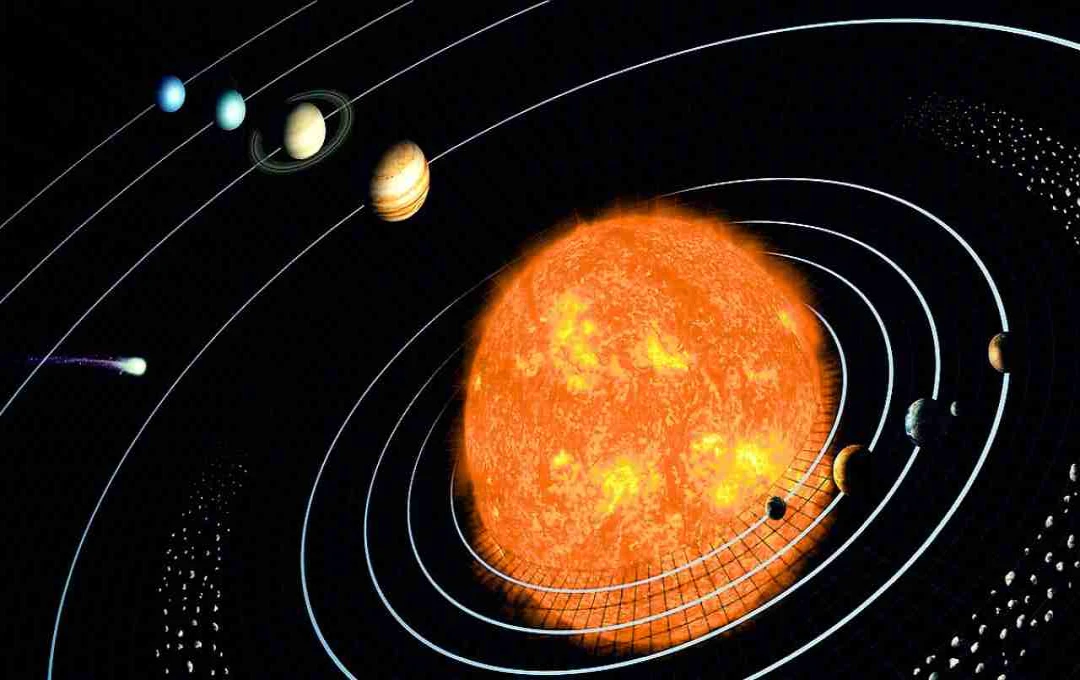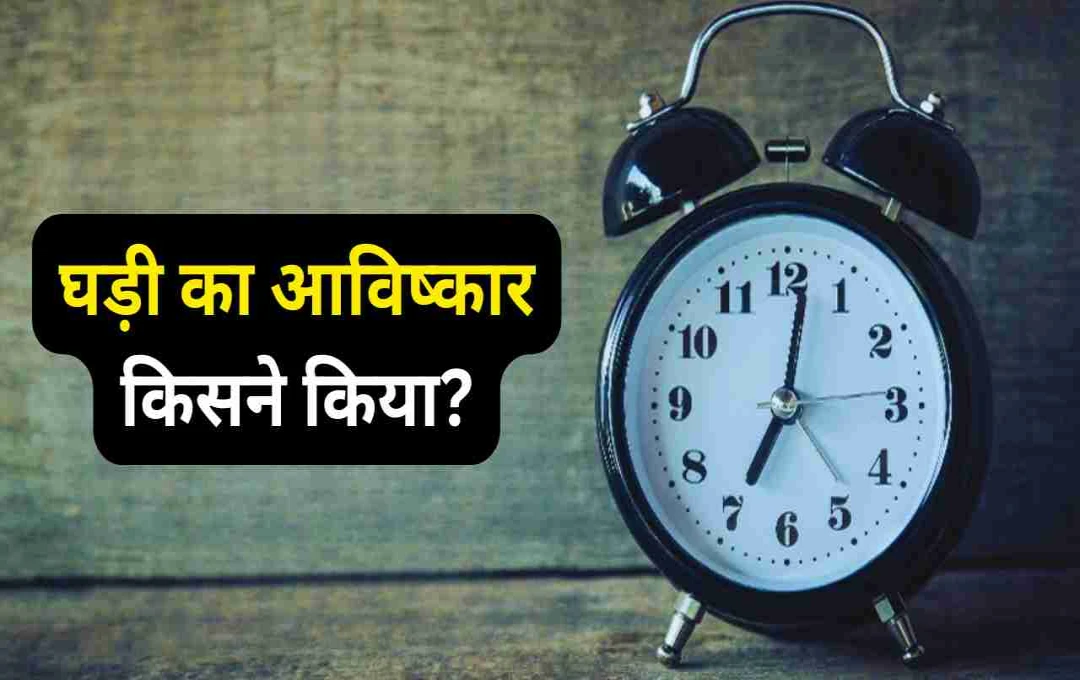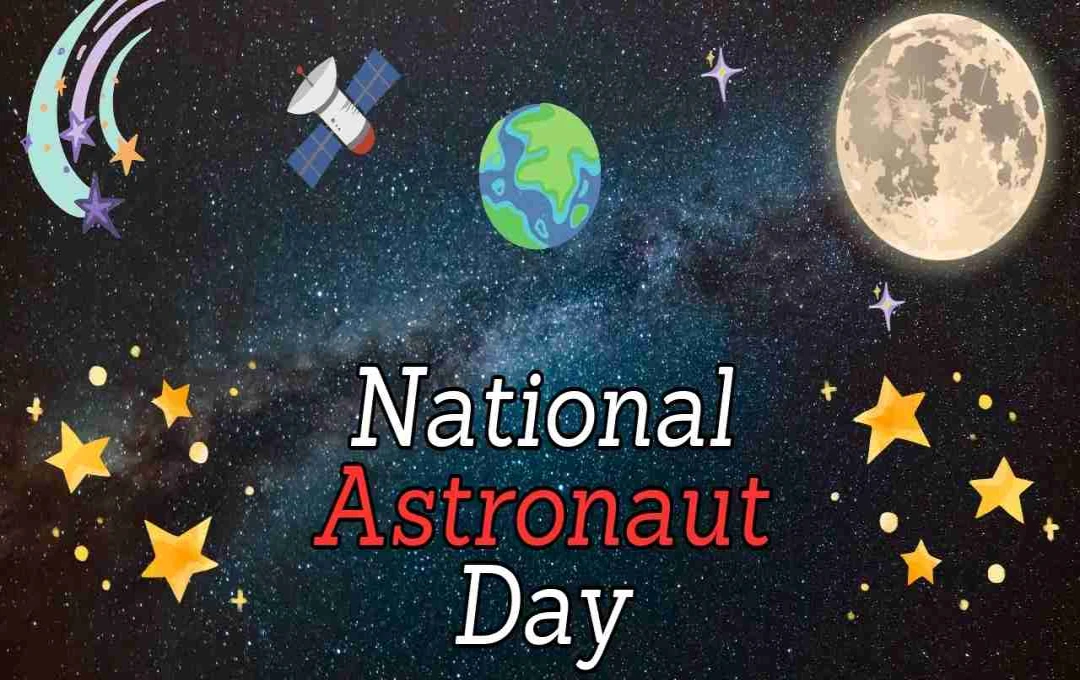মহাকর্ষ — একটি শব্দ যা আজ বিজ্ঞানের একটি সাধারণ অংশ, কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগে এটি একটি রহস্যময় শক্তি হিসাবে বিবেচিত হত। এটি দার্শনিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী পর্যন্ত সকলকে আকৃষ্ট করেছে। আজ আমরা যে বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর নির্ভর করি, তা বহু সভ্যতা এবং পণ্ডিতদের কয়েক হাজার বছরের গবেষণার ফল। আসুন, আমরা মহাকর্ষের এই ঐতিহাসিক এবং বৌদ্ধিক যাত্রাটি বুঝি।
গ্রিক দর্শনে মহাকর্ষের বীজ
মহাকর্ষের প্রাচীনতম ধারণাগুলি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল। হেরাক্লিটাস, এম্পেদোক্লিস এবং লিউসিপাসের মতো চিন্তাবিদরা এই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে মহাবিশ্ব এক প্রকার ভারসাম্য এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তির দ্বারা চালিত হয়। এম্পেদোক্লিস 'প্রেম' এবং 'সংঘাত'-কে মহাবিশ্বের দুটি মৌলিক শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, যার মধ্যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের চিত্র দেখা যায়। অ্যারিস্টটল মহাকর্ষকে একটি প্রাকৃতিক প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করতেন। তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে ভারী বস্তু নিচের দিকে এবং হালকা বস্তু উপরের দিকে যায়। তিনি পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র মনে করে সমস্ত ভারী বস্তুর গতিকে সেই দিকে নির্দেশিত করেছেন।
ভারতীয় পণ্ডিতদের অনন্য অবদান
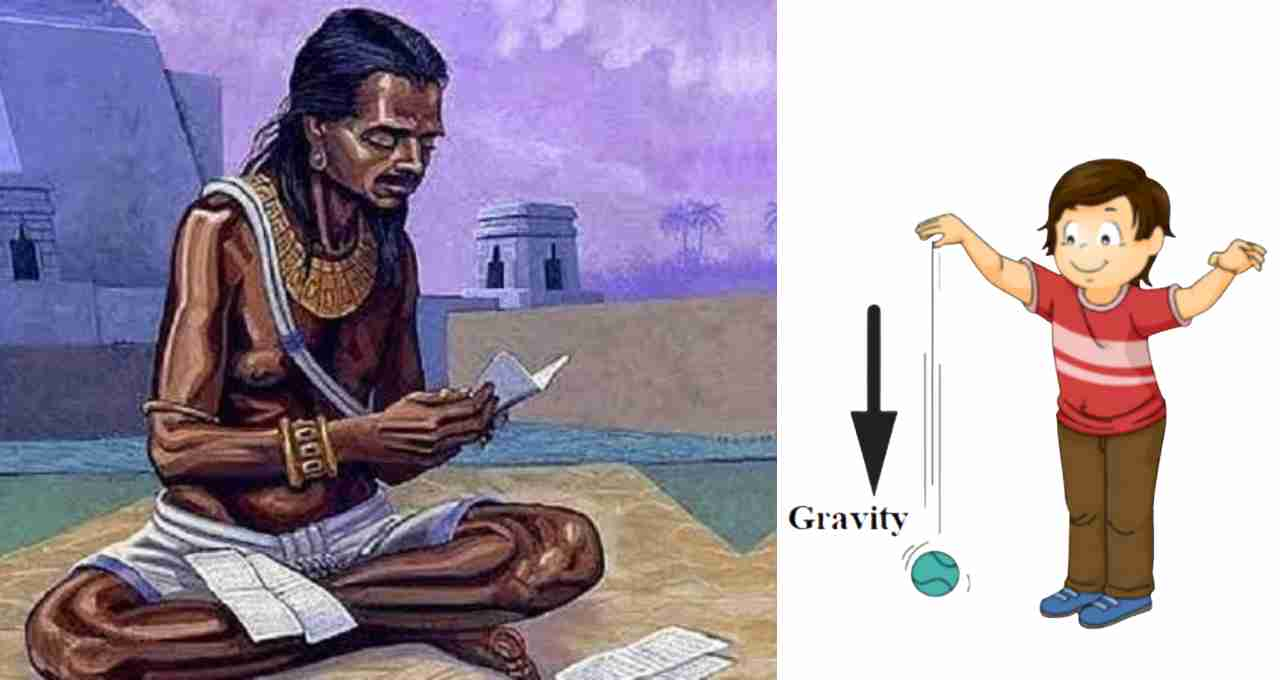
সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রহ্মগুপ্ত মহাকর্ষকে আকর্ষণের শক্তি হিসাবে প্রথম স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে 'পৃথিবীর বস্তুকে নিজের দিকে টানার প্রবণতা রয়েছে', যা আজকের 'গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স'-এর মূল ধারণা ছিল। একাদশ শতাব্দীর ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে বলেছেন, 'পৃথিবী বিনা অবলম্বনে থাকা বস্তুকে নিজের দিকে টানে।' এই উক্তিটি কেবল নির্ভুল ছিল তাই নয়, মহাকর্ষের আচরণকে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌত নিয়মে পরিণত করে। এটি ব্যাখ্যা করে যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তা সেই সময়েও কতটা পরিপক্ক ছিল।
ইসলামিক স্বর্ণযুগে মহাকর্ষের ব্যাখ্যা
ইসলামী বিশ্বের বিজ্ঞানীরাও মহাকর্ষের ধারণাকে আরও গভীর করেছেন। ১১শ শতাব্দীর ইবনে সিনা গতি এবং বলের মধ্যেকার সম্পর্ককে স্পষ্ট করেছিলেন। তাঁর প্রেরণা তত্ত্ব আইজ্যাক নিউটনের গতির সূত্রের পূর্বসূরি ছিল। ইবনে আল-হাইথাম এবং আল-বিরুনী পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুতেও মহাকর্ষের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। আল-খাজিনী প্রস্তাব করেছিলেন যে বস্তুর মহাকর্ষীয় বল তাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে, যা পরবর্তীতে নিউটনের মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের আবিষ্কারের সাথে যুক্ত হয়।
ইউরোপীয় রেনেসাঁস এবং নতুন আবিষ্কারের যুগ
১৪শ শতাব্দীতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। জ্যাঁ বুরিদান এবং আবুল-বারাকাত-এর মতো পণ্ডিতরা আবেগ (impetus)-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, যা গতি এবং ভরের মধ্যে সম্পর্কের একটি নতুন দিক ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে গ্যালিলিও গ্যালিলি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন যে সমস্ত বস্তু, তাদের ওজন যাই হোক না কেন, একই ত্বরণে পতিত হয়। এই তত্ত্ব অ্যারিস্টটলের ধারণার বিরুদ্ধে ছিল এবং মহাকর্ষের আধুনিক ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে।
আইজ্যাক নিউটন: আধুনিক মহাকর্ষ তত্ত্বের ভিত্তি
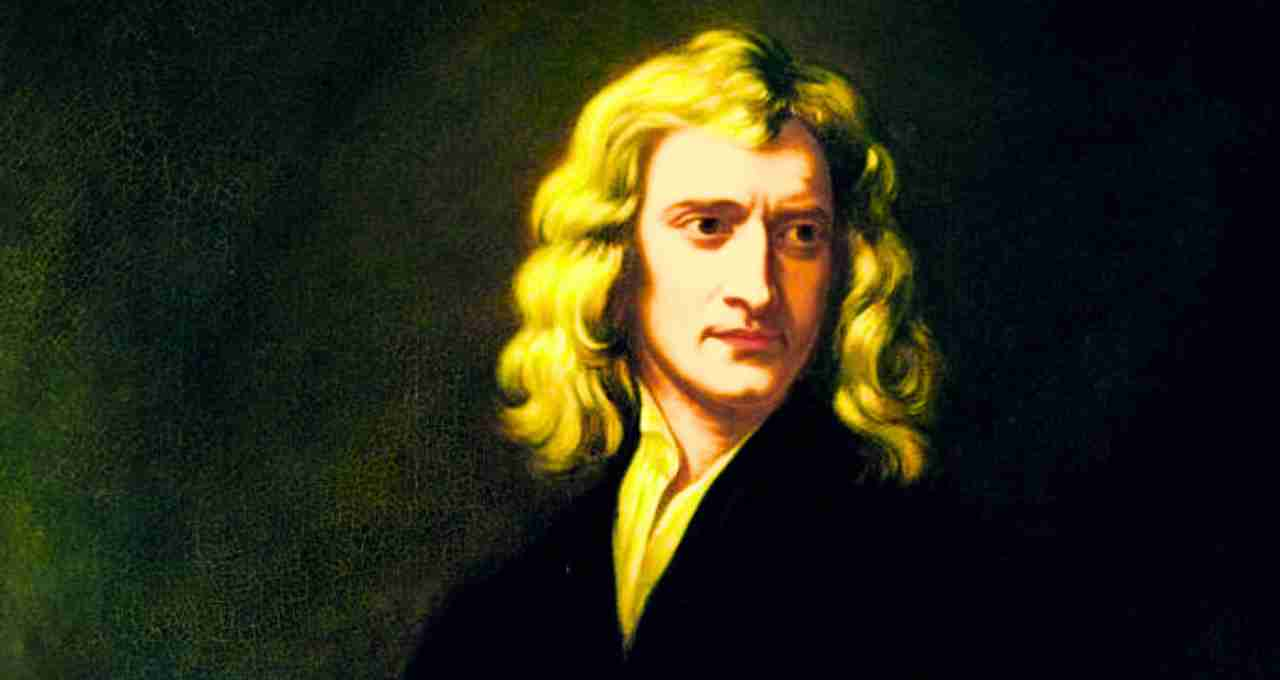
১৭শ শতাব্দীতে স্যার আইজ্যাক নিউটন ‘মহাকর্ষের সর্বজনীন নিয়ম’ (Law of Universal Gravitation) প্রতিপাদন করেন। তিনি বলেন যে প্রতিটি বস্তু, দ্বিতীয় বস্তুকে তার ভরের অনুপাতে আকর্ষণ করে এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়। নিউটনের এই নিয়ম কেবল সৌরজগৎ নয়, পুরো মহাবিশ্বের গতি ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Principia Mathematica বিজ্ঞানকে গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখিয়েছে এবং মহাকর্ষকে একটি অনুমান থেকে ভৌত নিয়মে রূপান্তরিত করেছে।
আইনস্টাইন এবং আপেক্ষিকতার যুগ
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আলবার্ট আইনস্টাইন নিউটনের তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity) দেখিয়েছে যে মহাকর্ষ কেবল একটি বল নয়, ভর এবং শক্তির কারণে স্থান-কালের বক্রতা (curvature of space-time)। তিনি প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর মতো বস্তু স্থান-কালকে বিকৃত করে এবং অন্যান্য বস্তু সেই বক্রতা অনুসরণ করে চলে। এই ধারণা আজও মহাবিশ্বের রহস্য বুঝতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে।
আধুনিক সময়ে মহাকর্ষের অনুসন্ধানের নতুন দিগন্ত
আজ বিজ্ঞানীরা স্ট্রিং থিওরি, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ এবং গ্র্যাভিটন-এর মতো ধারণার মাধ্যমে মহাকর্ষকে एकीकृत তত্ত্বের (Theory of Everything) সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। ২০১৫ সালে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের নিশ্চিতকরণ আইনস্টাইনের তত্ত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। এটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় ছিল।
মহাকর্ষের ধারণা প্রাচীন গ্রিক, ভারতীয়, ইসলামী এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অবদানের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, গ্যালিলিও, নিউটন এবং আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীরা এটিকে যথাক্রমে বল, নিয়ম এবং স্থান-কালের বক্রতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আজও বিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় শক্তির গভীরতা বুঝতে সচেষ্ট রয়েছেন।