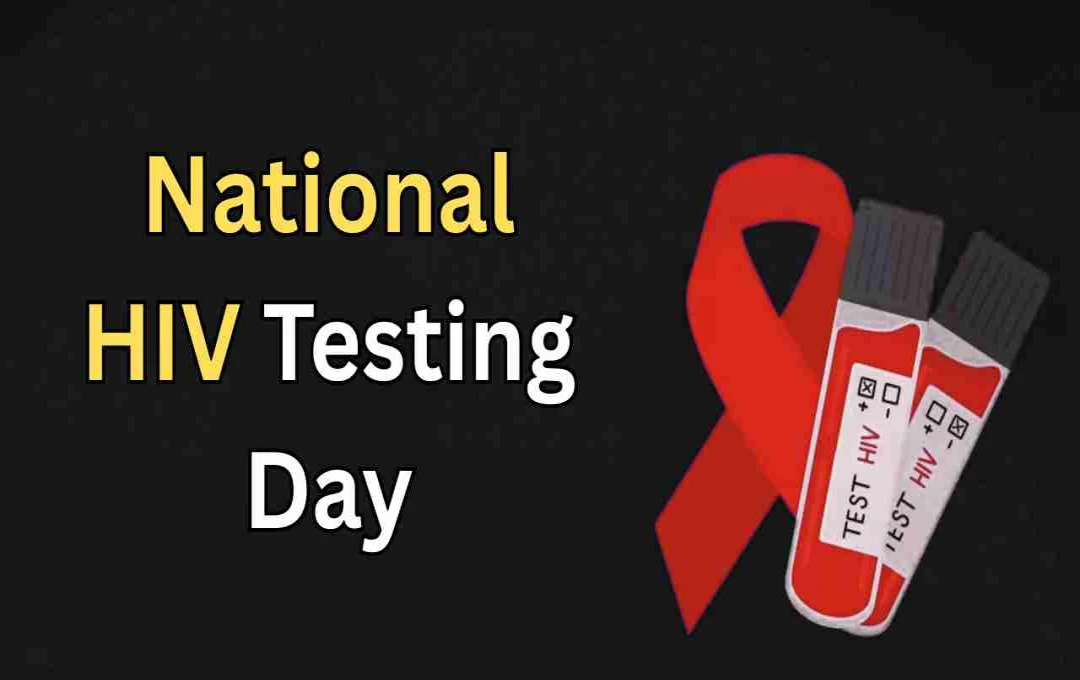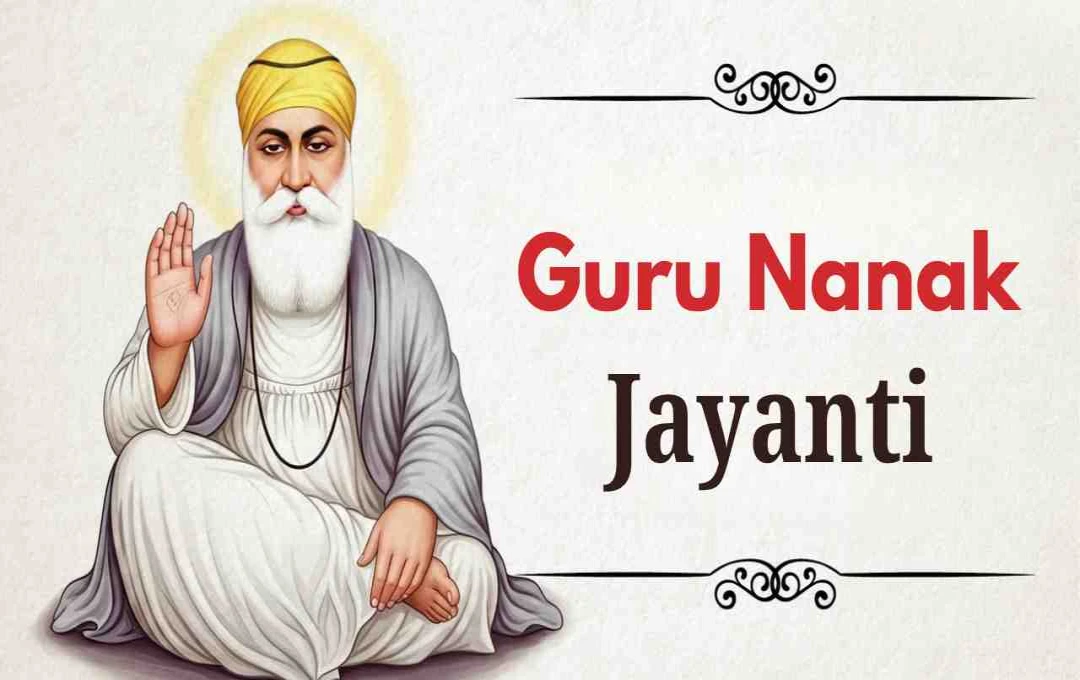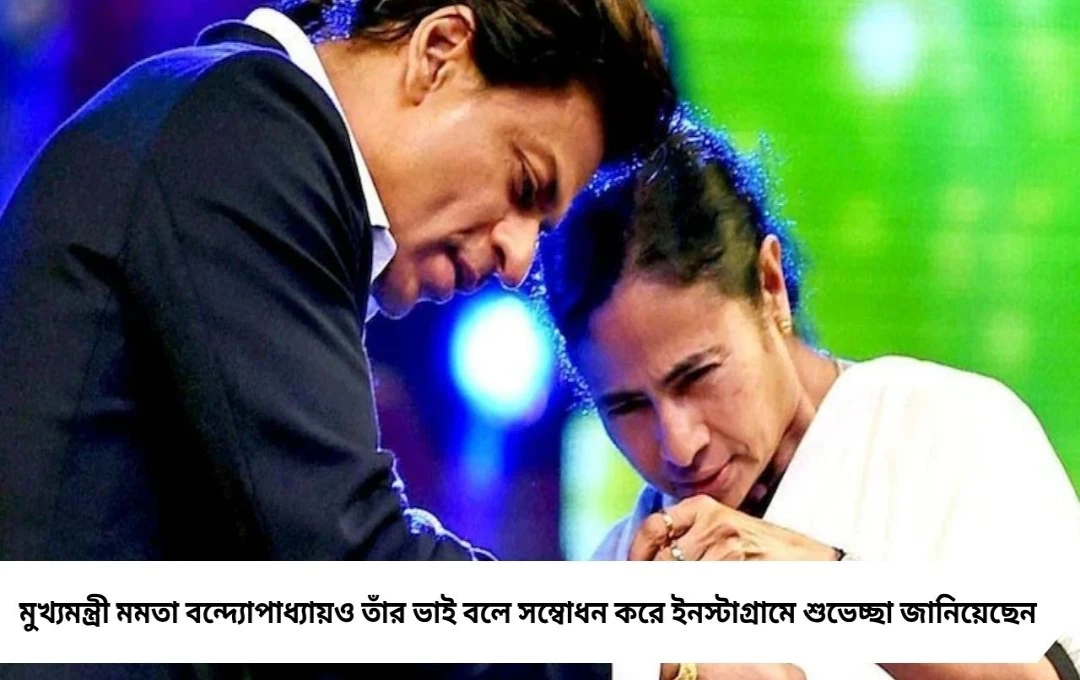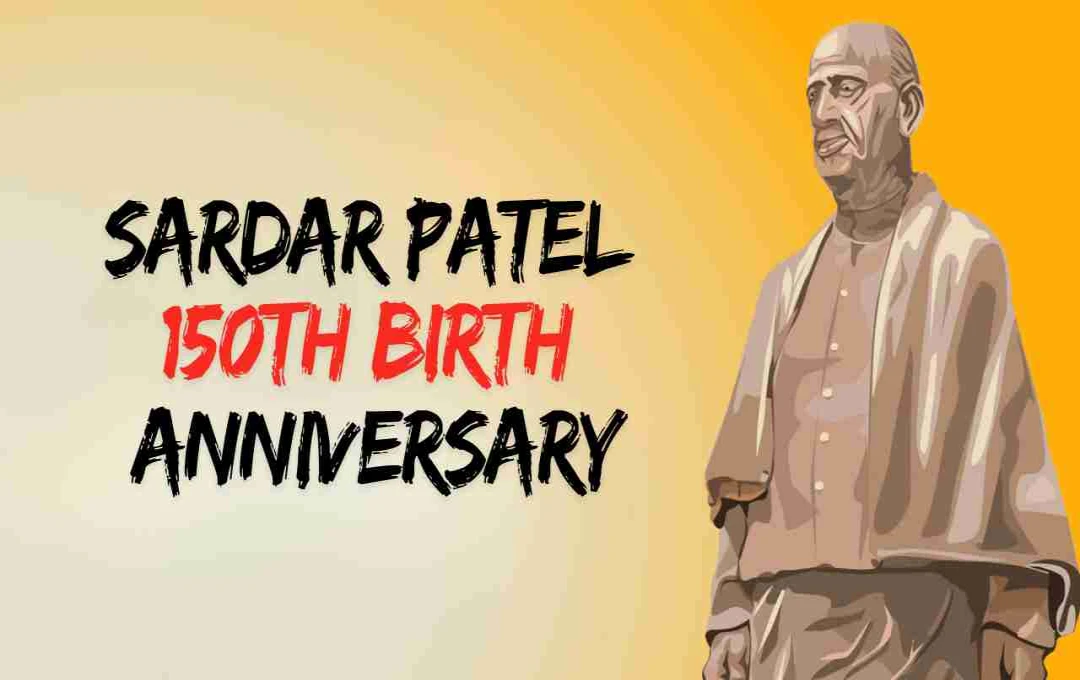ভারতীয় ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে, যাদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য এবং কল্পনার সংমিশ্রণে এক নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। জয়চন্দ্র, যিনি লোককথায় 'জয়চাঁদ' নামে পরিচিত, তেমনই একজন রাজা যাঁর ঐতিহাসিক কৃতিত্ব কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, এবং যাঁর ভাবমূর্তি একজন 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই নিবন্ধে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে জয়চন্দ্র কে ছিলেন, তাঁর শাসনকাল কেমন ছিল এবং কীভাবে একটি সাহিত্যিক রচনা তাঁর ঐতিহাসিক ভাবমূর্তিকে পরিবর্তন করে দিল।
শাসনের বিস্তার ও প্রভাব
জয়চন্দ্র ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর গাহাড়বাল রাজবংশের শেষ প্রভাবশালী সম্রাট। তাঁর রাজ্য কনৌজ এবং বারাণসীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সেই সময় গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য ছিল, যা আজকের পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বিহারের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন না, বরং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডেও গভীর আগ্রহ রাখতেন। তাঁর শাসনকালের অসংখ্য শিলালিপি, বিশেষ করে বারাণসী ও বোধগয়া অঞ্চলে, এই কথার প্রমাণ দেয় যে তিনি গ্রাম দান, মন্দির নির্মাণ এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো কাজে অবদান রেখেছিলেন।
প্রাথমিক জীবন এবং রাজ্যাভিষেক
জয়চন্দ্র গাহাড়বাল বংশের রাজা বিজয়চন্দ্রের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবনের বিবরণ সীমিত, কিন্তু কামাউলি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১১৭০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন তাঁকে রাজগদি অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর দাদু গোবিন্দচন্দ্রের উপাধিগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন, যেমন:
- অশ্ব-পতি নরা-পতি গজ-পতি রাজত্রয়ধিপতি — অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এবং হস্তী বাহিনীর অধিপতি।
- विविধ-বিদ্যা-বিচার-वाचस्पति — বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতার পরিচায়ক।
সেন বংশ ও ঘুরিদ আক্রমণ

জয়চন্দ্রের শাসনকালে দুটি প্রধান সামরিক সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমটি ছিল সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের আক্রমণ, যার ফলে জয়চন্দ্রকে মগধ থেকে পিছু হটতে হয়। দ্বিতীয় এবং নির্ণায়ক সংঘাতটি ছিল ঘুরিদ শাসক মুহাম্মদ ঘোরীর সঙ্গে। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে জয়চন্দ্র যমুনা নদীর তীরে গজনি থেকে আসা ৫০,০০০ ঘোড়সওয়ারের ঘুরিদ বাহিনীর सामना করেছিলেন। তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে নিহত হন। হাসান নিজামী এবং ফरिश्তা-র মতো ঐতিহাসিকদের মতে, যুদ্ধের সময় জয়চন্দ্র একটি হাতির উপর सवार ছিলেন এবং একটি তীর লাগার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।
সংস্কৃতি ও ধর্ম
জয়চন্দ্র শুধুমাত্র যুদ্ধের রাজা ছিলেন না, বরং সংস্কৃতি ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর রাজসভায় অনেক কবি ও পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। কবি ভট্ট কেদার এবং মধুकर তাঁর জীবনীর উপর কাব্য রচনা লিখেছিলেন, যদিও সেগুলি এখন दुर्लभ। ধর্মীয়ভাবে, জয়চন্দ্র ছিলেন এক জটিল ব্যক্তিত্ব। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে তিনি এক গুরুর কাছ থেকে কৃষ্ণ ভক্তি-তে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্যাভিষেকের পর তিনি 'পরম-মাহেশ্বর'-এর উপাধি গ্রহণ করে শৈব ধর্মকেও আপন করেছিলেন। इसके साथ ही, বোধগয়ায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে यह भी জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং বৌদ্ধ मठ निर्माण-এ सहयोग করেছিলেন।
পৃথ্বীরাজ রাসো: ইতিহাস নাকি কল্পনা?

জয়চন্দ্রের ভাবমূর্তিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে পৃথ্বীরাজ রাসো, যা চন্দ্রবরদাই লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁকে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি পৃথ্বীরাজ চৌহানের শত্রু ছিলেন এবং যিনি তাঁর পরাজয়ের জন্য মুসলিম আক্রমণকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।
তবে, এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে गंभीर প্রশ্ন ওঠে:
- জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাজের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাত শিলালিপিতে নথিভুক্ত নেই।
- 'সংযুক্তা'-র স্বয়ম্বর এবং অপহরণের কাহিনীরও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।
- পৃথ্বীরাজ বিজয়ের মতো সমসাময়িক গ্রন্থ রাসোর অনেক কথার খণ্ডন করে।
ঐতিহাসিকদের ধারণা, পৃথ্বীরাজ রাসো একটি জাতীয়তাবাদী বীররস রচনা, যার উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক ভারত বিজয়ের যন্ত্রণা কমানো এবং হিন্দু নায়কদের महिमामंडित করা। এমতাবস্থায় জয়চন্দ্রকে একজন "বিশ্বাসঘাতক" হিসেবে উপস্থাপন করা সেই সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিল।
‘জয়চাঁদ’ নামের উত্তরাধিকার
ইতিহাসের विडंबना यही है যে জয়চন্দ্র, যিনি একজন सशक्त, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে প্রबुद्ध রাজা ছিলেন, লোককথায় "দেশদ্রোহী" হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছেন। আজও কাউকে 'জয়চাঁদ' বলে দেওয়া, एक गहरे अपमान के रूप में लिया जाता है। यह उस ঐতিহাসিক अन्याय की याद दिलाता है, जहाँ मिथकों और साहित्यिक कल्पनाओं ने किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान को बदल दिया।
জয়চন্দ্র এমন একজন সম্রাট ছিলেন, যিনি তাঁর রাজ্যে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু গাহাড়বাল বংশের পতনের সূচনা করে এবং উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনের বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু, তাঁর মূল্যায়ন শুধুমাত্র 'বিশ্বাসঘাতকতা'-র দৃষ্টিকোণ থেকে করা, একটি ঐতিহাসিক ভুল। প্রয়োজন ইতিহাস এবং লোককথার মধ্যে পার্থক্য বোঝা এবং এমন শাসকদের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে বিচার করা।